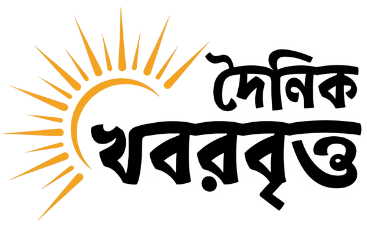ভূমিকা
পরিবেশ রক্ষা এখন আর কেবল একটি “আদর্শিক” বিষয় নয়—এটি মানবজীবনের অস্তিত্বের প্রশ্ন। নদী, বন, পাহাড়, জীববৈচিত্র্য, বায়ু—সবকিছুই আজ মারাত্মকভাবে বিপন্ন। পৃথিবীজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাব দৃশ্যমান, এবং বাংলাদেশও তার অন্যতম শিকার। এই প্রেক্ষাপটে কিছু সাহসী মানুষ এগিয়ে আসে—নদী বাঁচাও আন্দোলন, বন রক্ষা কমিটি, পাহাড় ধ্বংস রোধ, বা শিল্প দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে। তারা সাধারণ মানুষ, শিক্ষক, ছাত্র, কৃষক, সাংবাদিক, কিংবা সামাজিক কর্মী।
কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা যায়—যাদের উদ্দেশ্য প্রকৃতি ও মানুষের মঙ্গল রক্ষা করা, তারাই অনেক সময় হয়রানি, মামলা, গ্রেপ্তার, এমনকি প্রাণনাশের হুমকির শিকার হন। রাষ্ট্রীয় এবং কর্পোরেট স্বার্থের দ্বন্দ্বে পড়ে এই মানুষগুলো হয়ে ওঠেন “অপরাধী”। এই লেখায় আমরা দেখব—কেন এবং কীভাবে বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনকারীরা দমন-পীড়নের মুখে পড়ে, এবং এর সামাজিক ও নৈতিক পরিণতি কী।
পরিবেশ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর দেশ। নদী, মাটি ও বনভূমি এ দেশের জীবনীশক্তি। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের নামে এই সম্পদগুলো দ্রুত ধ্বংস হচ্ছে। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা—প্রায় প্রতিটি নদীই দূষিত বা দখলকৃত; সুন্দরবন হুমকির মুখে; পাহাড়ে নির্বিচারে পাথর কাটা ও বন উজাড় চলছে।
এই অবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ, পরিবেশবিদ ও স্থানীয় নাগরিকরা প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। তারা রাস্তায় নেমেছেন, মানববন্ধন করেছেন, আদালতে মামলা করেছেন, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতা ছড়িয়েছেন। তাদের অনেকেই “সবুজ যোদ্ধা” নামে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক স্বার্থের সংঘাতে তাদের অনেকের জীবন হয়ে পড়েছে বিপদসংকুল।
রাষ্ট্র ও কর্পোরেট স্বার্থের সংঘাত
একটি বড় বাস্তবতা হলো—পরিবেশ ধ্বংসের পেছনে প্রায়ই থাকে প্রভাবশালী গোষ্ঠী, কর্পোরেট বিনিয়োগকারী, এবং কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় প্রকল্প। যখন কোনো নাগরিক বা সংগঠন এই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তখন তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়।
যেমন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, নদী দখল, বা পাহাড় কাটা নিয়ে প্রতিবাদ করলে অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার বা হুমকি দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ আন্দোলনকারীরা বলেন—এটি একটি “সিস্টেমেটিক ভয়ভীতি প্রদর্শন” যার মাধ্যমে মানুষকে নীরব রাখতে চাওয়া হয়। রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি পরিবেশ ধ্বংসের দায়ে সমালোচিত হয়, তখন সেই সমালোচককেই “রাষ্ট্রবিরোধী” বলা হয়।
এই মনোভাব শুধু আইনি নয়, নৈতিকভাবেও বিপজ্জনক। কারণ যে সমাজে ভিন্নমত শোনা হয় না, সেই সমাজের উন্নয়ন কখনো টেকসই হয় না।
আইনি ও প্রশাসনিক দমননীতি
বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষায় কিছু আইন রয়েছে—যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, বন আইন, নদী রক্ষা কমিশন আইন ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে এই আইনগুলো প্রায়শই ব্যবহৃত হয় না, বরং কখনো কখনো উল্টো আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার হয়।
পরিবেশ কর্মীরা যখন শিল্প দূষণ বা ভূমি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, তখন স্থানীয় প্রশাসন তাদের “উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড”, “জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ”, কিংবা “রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ব্যাহত করার” অভিযোগে মামলা করে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকেও মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় অনলাইনে আন্দোলনের প্রচারণা ঠেকাতে।
এর ফলে পরিবেশ আন্দোলনকারীরা আতঙ্কের মধ্যে থাকেন—কখন তাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে, কখন পুলিশ ডেকে নেবে, কখন হয়তো স্থানীয় দখলদারদের হুমকি আসবে। অনেকেই তাই নিজের নাম গোপন রেখে কাজ করেন, কেউ কেউ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন।
সমাজে প্রতিক্রিয়া ও ভয়ের সংস্কৃতি
একটি বড় সমস্যা হলো—সাধারণ মানুষও অনেক সময় পরিবেশ আন্দোলনকে “উন্নয়নবিরোধী” বলে ভুল বোঝে। কারণ, তারা তাত্ক্ষণিক উন্নয়ন (রাস্তা, কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র) দেখেন, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি (বন ধ্বংস, পানি দূষণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়) বোঝেন না।
ফলে পরিবেশ রক্ষাকারীরা এক ধরনের সামাজিক একাকিত্বে পড়ে। তাদের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা তৈরি হয়—তারা “বিদেশি এজেন্ট”, “অগ্রগতির শত্রু”, কিংবা “অর্থনৈতিক অগ্রগতির বাধা”। এই ভয়ের সংস্কৃতি শুধু রাষ্ট্রীয় দমন নয়; এটি একটি সামাজিক নিপীড়নও, যা নীরবে তাদের গলা চেপে ধরে।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
বিশ্বজুড়ে পরিবেশ আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন নতুন কিছু নয়। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ফিলিপাইন—সব জায়গায় পরিবেশ রক্ষাকারীদের হত্যা, গুম, এবং আইনি হয়রানির ঘটনা বেড়েছে। গ্লোবাল উইটনেস নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৩ সালেই পৃথিবীজুড়ে ১৭৭ জন পরিবেশ কর্মী নিহত হয়েছেন।
বাংলাদেশেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নদী বাঁচাও আন্দোলন, তেল-গ্যাস খনিজ রক্ষা আন্দোলন, রামপাল-বিরোধী আন্দোলন—সব জায়গাতেই কর্মীরা হয়রানি ও আইনি বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। আন্তর্জাতিক মহল এই বিষয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, কিন্তু পরিবর্তন ধীর।
নারী পরিবেশ কর্মীদের বাড়তি ঝুঁকি
নারী পরিবেশকর্মীরা পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ ঝুঁকির মুখে পড়েন। তারা শুধু রাষ্ট্রীয় ও কর্পোরেট হুমকিই নয়, বরং সামাজিক অপমান, চরিত্রহনন, ও অনলাইন হয়রানিরও শিকার হন। অনেক নারী সাংবাদিক ও কর্মী বলেন—“আমরা শুধু বন বা নদীর কথা বলি না, বলি মানুষের বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু সমাজ সেটিকে হুমকি মনে করে।”
এই বৈষম্য তাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণকে আরও কঠিন করে তোলে। ফলে অনেকেই পিছু হটে যান, আর যারা টিকে থাকেন, তারা ভীত, একাকী ও মানসিক চাপগ্রস্ত জীবনযাপন করেন।
গণমাধ্যমের ভূমিকা
বাংলাদেশের গণমাধ্যম পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে, কিন্তু প্রায়শই “সতর্কভাবে”। বড় কর্পোরেট বিজ্ঞাপনদাতা বা রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা অনেক সময় সরাসরি লিখতে পারেন না।
তবে কিছু স্বাধীন সাংবাদিক ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সাহসিকতার সঙ্গে সত্য প্রকাশ করছেন। তবুও হুমকি, মামলা, বা সাংবাদিক নির্যাতনের কারণে পরিবেশ বিষয়ক অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা এখনো সীমিত।
দমন-পীড়নের সামাজিক ও মানসিক প্রভাব
পরিবেশ আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়নের প্রভাব শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে। মানুষ যখন দেখে, ন্যায়ের কথা বলার জন্য কেউ শাস্তি পায়—তখন নীরবতা ছড়িয়ে পড়ে। নাগরিক সমাজ দুর্বল হয়, স্বাধীন চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়।
অনেক তরুণ পরিবেশবিদ বলেন—“আমরা এখন কথা বলার আগে ভাবি, এটা পোস্ট করলে সমস্যা হবে কি না।” এই ভয়ই সবচেয়ে বড় পরাজয়। কারণ, যেখানে ভয় আছে, সেখানে আন্দোলন বা মানবতা টিকে থাকতে পারে না।
করণীয় ও ভবিষ্যৎ ভাবনা
পরিবেশ রক্ষা একটি বৈশ্বিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তির অংশীদার। তাই সরকারের উচিত পরিবেশ কর্মীদের সহযোগী হিসেবে দেখা, প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়।
কিছু সুপারিশ করা যেতে পারে—
-
আইনি সুরক্ষা: পরিবেশ আন্দোলনকারীদের জন্য বিশেষ আইনি সহায়তা ও নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক তৈরি করা।
-
প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা: প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের পরিবেশ বিষয়ক সংবেদনশীলতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
-
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: পরিবেশ বিষয়ক অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতাকে উৎসাহ দেওয়া।
-
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: জাতিসংঘ ও এনজিওগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে মানবাধিকার রক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা।
-
সামাজিক সচেতনতা: জনগণকে বোঝানো যে পরিবেশ রক্ষা মানে উন্নয়ন থামানো নয়; বরং টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।
উপসংহার
পরিবেশ আন্দোলনকারীরা কোনো রাষ্ট্রবিরোধী নয়; তারা প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রের বন্ধু। তারা আমাদের নদী, বন, পাহাড়, বাতাস ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। তাদের কণ্ঠরোধ মানে প্রকৃতির কণ্ঠরোধ।
আজ যারা “অগ্রগতির নামে” তাদের নিপীড়ন করছে, তারা হয়তো বুঝছে না—এই পৃথিবী, এই দেশ, এই প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ নেবে দূষণ, বন্যা, খরা, ও বিপর্যয়ের মাধ্যমে। তাই এখনই প্রয়োজন তাদের পাশে দাঁড়ানো, দমন নয়—সহযোগিতা।
পরিবেশ রক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়; এটি টিকে থাকার সংগ্রাম। আর যারা এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা কোনো অপরাধী নন—তারা মানবজাতির রক্ষাকর্তা। তাদের দমন করে আমরা আসলে নিজেদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছি।