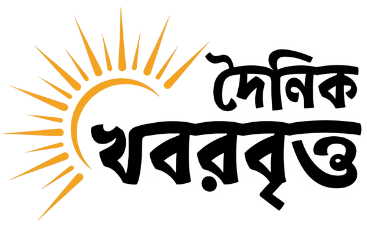আমাদের সমাজে “নিরাপত্তা” শব্দটি যত জোরে উচ্চারিত হয়, “স্বাধীনতা” শব্দটি ততটাই ফিসফিস করে বলা হয়। বলা হয়, নিরাপত্তার স্বার্থে কিছু অধিকার ছাড় দিতেই হবে। বলা হয়, রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখতে গেলে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই ছাড় কতদূর? আর এই নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত কাকে রক্ষা করে?
মানবাধিকার সংকট আজ আর শুধু নির্যাতনের দৃশ্যমান ঘটনাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে এক ধরনের মানসিক শাসনে, যেখানে মানুষ নিজেই নিজের সীমা আঁকতে শিখে যায়। কী বলা যাবে, কী বলা যাবে না—এই সিদ্ধান্ত আর রাষ্ট্র একা নেয় না; সমাজ, পরিবার, ধর্মীয় বয়ান এবং সামাজিক ভয়ের সংস্কৃতি মিলেই তা নির্ধারণ করে দেয়।
আমরা এমন এক বাস্তবতায় বাস করছি, যেখানে মানুষ কারাগারে না থেকেও বন্দি। কথা বলার আগে ভাবে, লিখবার আগে ভয় পায়, নিজের বিশ্বাস বা পরিচয় প্রকাশ করার আগে আশপাশের প্রতিক্রিয়া কল্পনা করে নেয়। এই আত্মনিয়ন্ত্রণকে অনেকেই শৃঙ্খলা বলে, কিন্তু বাস্তবে এটি এক ধরনের নীরব দমননীতি। মানবাধিকার এখানে প্রকাশ্যে খর্ব হয় না; ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়।
রাষ্ট্রের ক্ষমতা যখন নিরাপত্তার ভাষায় কথা বলে, তখন মানবাধিকার প্রায়ই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। “জাতীয় স্বার্থ”, “সামাজিক স্থিতিশীলতা” কিংবা “নৈতিক শুদ্ধতা”—এই শব্দগুলো এতটাই শক্তিশালী যে, এর বিপরীতে ব্যক্তির অধিকার তুচ্ছ মনে হতে থাকে। অথচ ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, নিরাপত্তার নামে অধিকার খর্ব করার প্রবণতা শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তাকেই দুর্বল করে।
বিশেষ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব সবচেয়ে স্পষ্ট। ভিন্নমত এখন আর শুধু ভিন্নমত নয়; তা হয়ে উঠছে সন্দেহের বিষয়। প্রশ্ন করা মানেই রাষ্ট্রবিরোধিতা, সমালোচনা মানেই শত্রুতা—এই সরলীকৃত বয়ান সমাজে দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। ফলে মানুষ চুপ থাকতে শেখে, কারণ চুপ থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ পথ।
এই নীরবতার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হলো প্রান্তিক মানুষ। যাদের কণ্ঠস্বর এমনিতেই দুর্বল, তাদের জন্য এই ভয় আরও গভীর। একজন সংখ্যালঘু নাগরিক, একজন ভিন্ন বিশ্বাসী মানুষ, একজন ভিন্ন জীবনধারায় বিশ্বাসী ব্যক্তি—তাদের জন্য নিরাপত্তার বয়ান প্রায়ই হুমকিতে পরিণত হয়। কারণ নিরাপত্তা এখানে সবার জন্য সমান নয়; এটি প্রায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠের আরাম নিশ্চিত করার হাতিয়ার।
মানবাধিকার প্রশ্নে আমাদের সমাজে একটি বড় ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে—সব অধিকার নাকি একরকম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিছু অধিকারকে “অপ্রয়োজনীয়”, “অপ্রাসঙ্গিক” কিংবা “বিলাসিতা” হিসেবে দেখানো হয়। বিশেষ করে যখন অধিকারগুলো শরীর, চিন্তা বা পরিচয়ের সঙ্গে জড়িত হয়, তখন সেগুলোকে সহজেই বিতর্কিত বানানো যায়। এই বাছাইয়ের রাজনীতিই মানবাধিকারের সার্বজনীন ধারণাকে ভেঙে দেয়।
আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, মানবাধিকার কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর দাবি নয়। এটি এমন এক ন্যূনতম নিশ্চয়তা, যা ছাড়া মানুষ কেবল টিকে থাকে—বাঁচে না। কিন্তু যখন রাষ্ট্র বা সমাজ সিদ্ধান্ত নেয় কোন মানুষ “গ্রহণযোগ্য” আর কোন মানুষ “সমস্যা”, তখন মানবাধিকার আর অধিকার থাকে না; তা হয়ে ওঠে অনুগ্রহ।
এই অনুগ্রহের রাজনীতি সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ এতে অধিকার চাওয়াটাই অপরাধের মতো মনে হয়। মানুষ কৃতজ্ঞ হতে শেখে নিপীড়নের মধ্যেও। বলা হয়, “এর চেয়েও খারাপ হতে পারত”, “কমপক্ষে বেঁচে তো আছো”—এই বাক্যগুলো মানবাধিকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে অন্যায়ের মানদণ্ড ক্রমেই নিচে নেমে যায়।
ধর্ম, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ব্যাখ্যা এখানে বড় ভূমিকা রাখে। এগুলো মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সমস্যা শুরু হয় যখন এগুলো প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে। তখন মানবাধিকার আর নৈতিকতার আলোকে বিচার হয় না; বরং নৈতিকতা দিয়েই মানবাধিকার বিচার করা হয়। ফলে মানুষের কষ্ট গৌণ হয়ে যায়, আর নিয়মই মুখ্য হয়ে ওঠে।
একজন লেখক হিসেবে এই বাস্তবতা লিখতে গিয়ে সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো—ভাষা নির্বাচন। সরাসরি বললে বিপদ, ঘুরিয়ে বললে সত্যের ক্ষতি। এই দ্বন্দ্বেই লেখালেখি আজ এক ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তবুও লেখা জরুরি, কারণ নীরবতা কখনো নিরপেক্ষ নয়। নীরবতা প্রায়ই নিপীড়কের পক্ষ নেয়।
অনেকে বলেন, এসব লেখা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অস্থিরতা কি প্রশ্ন থেকে আসে, নাকি অন্যায় থেকে? যদি প্রশ্ন করলেই অস্থিরতা হয়, তাহলে সমস্যাটা প্রশ্নে নয়—সমস্যাটা সেই কাঠামোয়, যা প্রশ্ন সহ্য করতে পারে না। একটি সুস্থ সমাজ প্রশ্নকে ভয় পায় না; বরং প্রশ্ন থেকেই সে নিজেকে সংশোধন করে।
মানবাধিকার রক্ষার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো ভয়। ভয় মানুষকে চুপ করায়, একা করে, সন্দেহপ্রবণ করে তোলে। এই ভয় ছড়াতে খুব বেশি শক্তি লাগে না; কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। একজনকে দমন করলেই বাকিরা শিখে যায় কোথায় থামতে হবে। এই শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক না হলেও কার্যকর।
আমাদের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক ঘটনা নথিবদ্ধই হয় না। কারণ মানুষ অভিযোগ করতে ভয় পায়। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা, সামাজিক চাপ, রাজনৈতিক পরিচয়—সব মিলিয়ে ন্যায়বিচার অনেকের কাছে কেবল তাত্ত্বিক ধারণা। এই পরিস্থিতিতে মানবাধিকার নিয়ে কথা বলা অনেকের কাছে বিলাসিতা মনে হয়।
কিন্তু বাস্তবতা হলো—মানবাধিকার ছাড়া উন্নয়ন অর্থহীন। অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অবকাঠামো, প্রযুক্তি—সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে পড়ে, যদি মানুষ নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন না পায়। উন্নয়ন যদি কেবল সংখ্যায় মাপা হয়, আর মানুষের অভিজ্ঞতা উপেক্ষিত থাকে, তাহলে সেই উন্নয়ন একপাক্ষিক।
এই লেখার উদ্দেশ্য কাউকে অভিযুক্ত করা নয়; বরং একটি অস্বস্তিকর বাস্তবতার দিকে তাকাতে বাধ্য করা। আমরা কী ধরনের সমাজ গড়ে তুলছি, আর কোন মূল্য দিয়ে তা অর্জন করছি—এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলে ভবিষ্যৎ আরও সংকীর্ণ হবে। মানবাধিকার কোনো চূড়ান্ত অর্জন নয়; এটি প্রতিদিন নতুন করে রক্ষা করতে হয়।
শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি খুব সহজ—আমরা কি এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে মানুষ ভয় পেয়ে ভালো নাগরিক হয়? নাকি এমন একটি সমাজ, যেখানে মানুষ নিরাপদ বোধ করে সৎ নাগরিক হতে পারে? এই দুইয়ের পার্থক্যই মানবাধিকারের প্রকৃত মানদণ্ড।
লেখা হয়তো কিছু বদলায় না, কিন্তু লেখা না হলে কিছুই বদলানোর সুযোগ থাকে না। তাই এই কথাগুলো বলা জরুরি—অস্বস্তিকর হলেও, বিতর্কিত হলেও। কারণ মানবাধিকার নিয়ে নীরব থাকা মানেই একদিন নিজের অধিকার হারানোর প্রস্তুতি নেওয়া।
Md Abdur Rahman | Writer & Blogger