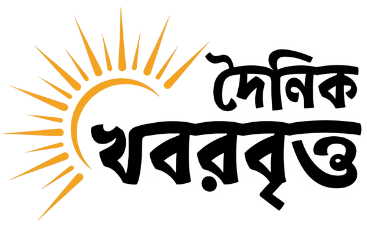বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের এক অখ্যাত গ্রাম। নামটা বলা ঠিক হবে না— শুধু এটুকু বলা যায়, এখানে ধর্মের নামে বিভাজনটা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায় প্রতিটি নিঃশ্বাসে।
গ্রামের দক্ষিণ দিকের ছোট্ট পাড়াটায় প্রায় পঞ্চাশটি হিন্দু পরিবার বাস করে। এদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসেছে প্রায় দুইশ বছর আগে। জমি চাষ করেছে, নদীতে মাছ ধরেছে, মেলা করেছে, গ্রামীণ নাটক খেলেছে। একসময় গ্রামের ঈদ আর পূজার উৎসব ছিল সবার। কিন্তু এখন, সেখানে আছে কেবল নীরবতা, অচেনা দেয়াল, আর এক অদৃশ্য ভয়।
“আমার ছেলেকে ক্লাসে বসতে দেয়নি”
মন্দিরপাড়ার কৃষক মনোরঞ্জন পাল বলেন, তাঁর ছেলে শুভ (১১) একদিন স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। ধর্মীয় শিক্ষার সময় শিক্ষক তাকে ক্লাসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। শুভর অপরাধ — সে মুসলমান নয়।
“ছোট ছেলেটা বোঝে না এসব কেন হয়,” মনোরঞ্জন বললেন, “ও শুধু বলেছিল, আমিও শিখতে চাই। কিন্তু শিক্ষক বললেন, ‘তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও’। এরপর থেকে ও স্কুলেই যেতে চায় না।”
এই গল্পটা এখন গ্রামের বাইরে ছড়িয়েছে। কেউ কেউ বলে— ‘মিডিয়া বানানো’, কেউ বলে— ‘ভুল বুঝেছে’। কিন্তু শুভর মুখের ভয়টা মিথ্যা নয়। স্কুলের সামনে তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বাবার চোখে এক ধরনের পরাজয় দেখা যায়, যা কোনো সংবাদ ছবিতে ধরা যায় না।
“ধর্মের কথা বললেই শত্রু হয়ে যাই”
গ্রামের উত্তরপাড়ার হোসেন মোল্লা, স্থানীয় চায়ের দোকান চালান। তিনিও চুপচাপ কণ্ঠে বললেন,
“আমরা আগে সবাই একসঙ্গে থাকতাম। এখন কেউ কারও বাড়িতে যায় না। ধর্মের কথা উঠলেই মনে হয়, আমি কিছু ভুল বলব, কেউ রাগ করবে।”
হোসেনের ছেলে স্থানীয় যুব সংগঠনে কাজ করে, কিন্তু কিছুদিন আগে তাকে বলা হয় “সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করতে।” হোসেন বলেন, “আমি জানি না কারা এসব চালায়, কিন্তু এটা ধীরে ধীরে সবাইকে আলাদা করে দিচ্ছে।”
মন্দিরে হামলার পর নীরবতা
২০২২ সালের অক্টোবরে দুর্গাপূজার সময় এক রাতে গ্রামের ছোট্ট মন্দিরে পাথর ছোড়া হয়। ভোরে দেখা যায়, গেট ভাঙা, ফুলছড়ার প্রতিমা নষ্ট।
পুরোহিত হরিপদ ভট্টাচার্য বলেন,
“যারা করেছে, তারা জানে কেউ কিছু বলবে না। থানায় গিয়েছিলাম, তারা বলল ‘অপর্যাপ্ত প্রমাণ’। তারপর থেকে রাতে ঘুমাই না। প্রার্থনা করতে ভয় লাগে।”
মন্দিরপাড়ার মহিলারা এখন রাতে একা বাইরে বের হয় না। পূজার রাতে আর আলো জ্বলে না আগের মতো। বাতাসেও একটা শূন্যতা।
“অভিযোগ দিলে বিপদে পড়ব”
স্থানীয় এক তরুণ হিন্দু ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন,
“আমি থানায় যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু গ্রামের এক প্রভাবশালী মুসলমান এসে বলল— ‘তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করো না, দোকানটা চালাতে দিব না।’”
এরপর সে আর অভিযোগ দেয়নি। এখন সে প্রতিদিন দোকানের পাশে বসে নীরবে ব্যবসা চালায়, কিন্তু ভয়টা থেকে গেছে।
“বড় বড় কথা শুনি টেলিভিশনে— ধর্মীয় সম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িক ঐক্য। কিন্তু এখানে আমরা জানি, কখন চুপ থাকতে হয়।”
স্কুল ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বৈষম্য
গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন,
“কিছু অভিভাবক আসে, বলে তাদের ছেলেমেয়েদের পাশে যেন হিন্দু বাচ্চারা না বসে। আমি বলি, এটা ঠিক না, কিন্তু বললে তারা ইউনিয়নে অভিযোগ দেয়, ‘শিক্ষক ধর্ম নষ্ট করছে’। আমরা টিকব কীভাবে?”
পূজোর সময় গ্রামের হিন্দু পরিবারগুলো আলাদা হয়ে যায়। ঈদের সময়ও কেউ তাদের বাড়িতে দাওয়াত দেয় না।
“আগে আমরা একসঙ্গে ভাত খেতাম, এখন কেউ চোখে চোখ রাখে না,” বলেন ষাটোর্ধ্ব কৃষ্ণরাম মজুমদার।
“এটা যুদ্ধ না, কিন্তু একটা নীরব বিচ্ছিন্নতা। কেউ আমাদের মারে না, কিন্তু পাশে দাঁড়ায়ও না।”
প্রশাসনের নীরবতা
উপজেলা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন,
“ধর্মীয় ইস্যু খুব সেনসিটিভ, রিপোর্ট লেখার আগে যাচাই করে নেওয়া দরকার।”
যখন জানতে চাই, সংখ্যালঘু পরিবারগুলো অভিযোগ করেও কেন সাড়া পায়নি, তিনি শুধু বলেন,
“আমাদের ওপরও রাজনৈতিক চাপ আছে।”
স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন,
“আমরা তদন্ত করছি, কিন্তু এই রিপোর্ট প্রকাশ হলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়াতে পারে।”
প্রশ্ন হলো — উত্তেজনা কে ছড়ায়? সত্য বলার মানুষ, না অন্যায়ের নীরব সমর্থকরা?
ইতিহাসের ভার
এই গ্রাম একসময় মুক্তিযুদ্ধের সময় আশ্রয় দিয়েছিল আশপাশের মুসলমান প্রতিবেশীদের। অনেকের বাড়ি ছিল একে অপরের আস্থার জায়গা।
কিন্তু এখন সেই ইতিহাসকেও ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের বয়স্কদের কাছে শুনলাম, ৭১-এ হরিপদ পাল নিজের বাড়িতে তিন মুসলমান পরিবারকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।
তিনি এখন বলেন,
“আমি তখন ভয় পাইনি, এখন পাই। কারণ তখন শত্রু ছিল বিদেশি, এখন শত্রু আমাদের ভেতরেই।”
“আমরা কারও ক্ষতি চাই না”
মন্দিরপাড়ার এক বৃদ্ধা বললেন,
“আমরা কারও ক্ষতি চাই না। শুধু শান্তিতে থাকতে চাই। কিন্তু যদি সত্য বলাই অপরাধ হয়, তাহলে আমরা কোথায় যাব?”
ধর্মীয় স্বাধীনতা তখনই বাস্তব, যখন কেউ ভয় ছাড়াই তার বিশ্বাস পালন করতে পারে।
এই গ্রামে এখন ভয়ই ধর্ম হয়ে গেছে— এমন এক ধর্ম, যা মানুষকে চুপ থাকতে শেখায়, প্রতিবেশী থেকে দূরে রাখে, এবং সত্য বলাকে বিপদে ফেলে।
ধর্মীয় স্বাধীনতা নাকি সামাজিক ভয়?
বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্ট লেখা আছে— প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবতার গ্রামে সেই অধিকার কাগজে থাকে, জীবনে নয়।
ধর্মীয় বৈষম্য এখন আর প্রকাশ্য হামলা নয়, বরং এক নীরব প্রাচীর, যা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে।
যখন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নীরব থাকে, শিক্ষক ভয়ে চুপ থাকে, আর প্রতিবেশী মুখ ফিরিয়ে নেয়— তখন ধর্মীয় স্বাধীনতা শুধু আইনি বাক্য হয়, জীবনের সত্য নয়।
শেষ বাক্য:
ধর্মীয় স্বাধীনতা কোনো অনুগ্রহ নয়— এটা মানুষের মৌলিক অধিকার।
যে সমাজে সত্য বলা বিপজ্জনক, সেখানে ধর্ম নয়, ভয়ই সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে।