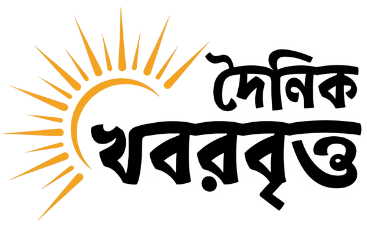মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন—এই কথাটি আমরা বইয়ে পড়ি, বক্তৃতায় শুনি, পোস্টারে দেখি। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা যেন এক অদৃশ্য বিলাসিতা। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা যখন প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও তথ্যপ্রবাহের চূড়ায়, তখনও মানুষ নিজের মতামত, বিশ্বাস, বা ভালোবাসা প্রকাশ করতে ভয় পায়। ভয়—রাষ্ট্রের, সমাজের, কিংবা ধর্মীয় মানদণ্ডের। এই ভয়ই আজ মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় শত্রু।
বাংলাদেশে মানবাধিকারের আলোচনা সবসময়ই সীমিত কিছু কণ্ঠে আটকে থাকে। যারা এসব বিষয়ে কথা বলেন, তারা হয় “বিদেশি এজেন্ট” তকমা পান, না হয় “ধর্মবিদ্বেষী” বা “রাষ্ট্রবিরোধী” পরিচয়ে অভিযুক্ত হন। অথচ মানবাধিকার কোনো বিদেশি ধারণা নয়—এটি মানুষের সবচেয়ে মৌলিক বাস্তবতা।
খাদ্য, শিক্ষা, মতপ্রকাশ, ধর্মাচার, যৌন স্বাধীনতা—এসব কেবল আইন নয়, মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত।
কিন্তু আমাদের সমাজে এই ন্যূনতম শর্তগুলো কতটা মানা হয়?
একজন শ্রমিক যদি ন্যায্য মজুরি দাবি করে, সেটিও “অরাজকতা” বলে চিহ্নিত হয়।
একজন নারী নিজের শরীর ও জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে তাকে “অশালীনতা”র অভিযোগে বিচার করা হয়।
একজন তরুণ যদি অন্য ধর্ম বা মতের প্রতি সহনশীলতা শেখায়, তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়।
আর কেউ যদি নিজের যৌন পরিচয় প্রকাশ করে, তাহলে তো সমাজের চোখে সে এক ‘অপরাধী’।
এই অবস্থায় মানবাধিকার কেবল আন্তর্জাতিক দিবসের ব্যানারে রয়ে গেছে। বাস্তব জীবনে এর কোনো স্থান নেই।
বাংলাদেশের সংবিধান বলছে—সব নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমরা দেখি, এই স্বাধীনতা কেবল “প্রশংসা করার স্বাধীনতা” পর্যন্ত সীমিত। সমালোচনা, প্রশ্ন, বা দ্বিমত প্রকাশের জায়গা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে।
একজন লেখক যদি সমাজের কোনো প্রচলিত চিন্তাকে প্রশ্ন করেন, তখন তার লেখা “ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত” বলে মামলা হয়।
একজন সাংবাদিক সত্য প্রকাশ করলে তাকে “রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট” করার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
এই পরিস্থিতি শুধু আইনি নয়—একটা সাংস্কৃতিক নীরবতা তৈরি করেছে। মানুষ মনে মনে জানে, সত্য বলা বিপজ্জনক। তাই সবাই চুপ করে যায়।
এই চুপ করে যাওয়ার সংস্কৃতিই সবচেয়ে ভয়ংকর। কারণ এখানেই মৃত্যু হয় মানবাধিকারের আসল আত্মার।
ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিও আজ ভয় ও রাজনীতির মধ্যে আটকে গেছে।
কোনো ব্যক্তি তার ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করুক, বা ধর্ম পালন না করুক—দু’ক্ষেত্রেই তাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়।
ধর্মকে ভালোবাসা এবং ধর্মের নামে অন্যায়কে প্রশ্ন করা—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আজ অনেকেই বোঝে না।
যারা ধর্মের নামে সহিংসতা, বৈষম্য বা নারীবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লেখেন, তাদের সহজেই “নাস্তিক” তকমা দেওয়া হয়।
কিন্তু প্রশ্নটা আসলে নাস্তিকতা নয়, প্রশ্নটা হলো মানবিকতা—কেউ কি মানুষের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে অন্যের বিশ্বাসের শত্রু হয়ে যায়?
যারা সত্যিকারের ধর্মপ্রাণ, তারা জানেন—প্রতিটি ধর্মেই মানবাধিকারের কথা বলা আছে।
কোনো ধর্মই অন্যায়, সহিংসতা বা ঘৃণাকে প্রশ্রয় দেয় না।
তবুও কিছু মানুষ ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছে। এই অপব্যবহার যখন নীতি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সমাজে ভয় তৈরি হয়। মানুষ ধর্মের নাম শুনে ভক্তি নয়, শঙ্কা অনুভব করে।
আর যৌন অধিকার—এটি তো আরও গভীর নীরবতার মধ্যে ঢাকা।
বাংলাদেশের অনেক তরুণ-তরুণী আজও নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে বাঁচতে বাধ্য।
তারা জানে, যদি কেউ জানতে পারে যে তারা সমকামী বা ভিন্ন যৌন পরিচয়ের, তাহলে চাকরি, পরিবার, এমনকি জীবন—সবকিছু হারাতে হতে পারে।
এই সমাজ এখনো মনে করে, ভালোবাসার একটা নির্দিষ্ট রঙ থাকা উচিত; কিন্তু ভালোবাসার তো কোনো রঙ নেই, কোনো ধর্ম নেই, কোনো সীমান্ত নেই।
মানবাধিকারের ধারণা বলে—প্রত্যেক মানুষ তার শরীর, চিন্তা ও ভালোবাসার ওপর নিজস্ব অধিকার রাখে।
রাষ্ট্র বা সমাজ কারও সেই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।
কিন্তু আমরা দেখি, যৌন পরিচয়ের প্রশ্নে রাষ্ট্র নীরব, সমাজ আক্রমণাত্মক, আর পরিবার লজ্জিত।
এই ত্রিমুখী চাপ একজন মানুষকে নিজের অস্তিত্ব থেকেই পালাতে বাধ্য করে।
এটাই সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন—যখন মানুষকে নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ দেওয়া হয় না।
কিছু মানুষ বলবেন—“আমাদের সমাজ এই ধরনের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত নয়।”
প্রশ্ন হলো, প্রস্তুত কে তৈরি করবে?
যখনই কেউ নতুন কোনো চিন্তা আনে, তখনই সমাজ বলে, “এটা এখনই সম্ভব নয়।”
কিন্তু পরিবর্তন কখনোই ‘প্রস্তুতি’ দেখে আসে না।
মানবাধিকারের ইতিহাসই হলো সাহসী মানুষের ইতিহাস—যারা অসময়ে সত্য বলেছে, যারা জনপ্রিয় হতে নয়, ন্যায়ের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে।
তারা অনেকেই অপমানিত হয়েছে, নির্বাসিত হয়েছে, কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছে।
কিন্তু তাদের বলা শব্দগুলোই আজ আমাদের সংবিধানে লেখা আছে, আমাদের বিবেকে জায়গা করে নিয়েছে।
মানবাধিকারের লড়াই কোনো এক দিনের, কোনো এক শ্রেণির নয়।
এটা প্রতিদিনের লড়াই—যখন কোনো শ্রমিক ন্যায্য মজুরি চায়,
যখন কোনো মা মেয়ের শিক্ষার অধিকার রক্ষায় সংগ্রাম করে,
যখন কোনো সাংবাদিক সত্য প্রকাশে ভয় পায় না,
যখন কোনো তরুণ ভালোবাসার স্বাধীনতা চায়—
তখনই মানবাধিকার বাস্তব রূপ পায়।
এই লড়াই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, অন্য ধর্ম বা সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও নয়;
এই লড়াই ভয়, নীরবতা, এবং অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে।
বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে, কিন্তু মানবাধিকারের পরিমাপে আমরা এখনো হাঁটছি কাঁচা পথে।
বক্তৃতায় উন্নয়ন যত জোরে বাজে, বাস্তব জীবনে ততটাই ক্ষীণ হয়ে আসে মানুষের কণ্ঠস্বর।
একজন মা তার সন্তান হারিয়ে বিচার চায়, তাকে বারবার দৌড়াতে হয়।
একজন সাংবাদিক নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ করে হয়রানির শিকার হন।
একজন নারী ধর্ষণের অভিযোগ তুলে প্রতিশোধের মুখে পড়ে।
একজন তরুণ সোশ্যাল মিডিয়ায় মতামত লিখে গ্রেপ্তার হয়।
এসব দৃশ্য আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা, অথচ এগুলো নিয়ে আমরা আর বিস্মিত হই না—এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পরাজয়।
মানবাধিকারকে আমরা যতটা আইন দিয়ে সংজ্ঞায়িত করি, তার চেয়ে অনেক বেশি সংজ্ঞা তৈরি হয় সংস্কৃতির মধ্যে।
আমাদের পরিবার, স্কুল, ধর্মীয় শিক্ষা—সব জায়গায় আমরা শিখি আনুগত্য, কিন্তু খুব কম শিখি প্রশ্ন করতে।
প্রশ্ন করার অভ্যাস না থাকলে মানবাধিকার থাকে কেবল বইয়ের পাতায়।
কারণ মানবাধিকার মানে কেবল অধিকার পাওয়া নয়, অন্যের অধিকারকেও স্বীকৃতি দেওয়া।
যে সমাজ অন্যের স্বাধীনতাকে সহ্য করতে পারে না, সে সমাজ কখনোই নিজের স্বাধীনতাও টিকিয়ে রাখতে পারে না।
আজ যখন পৃথিবীর নানা প্রান্তে মানুষ যুদ্ধ, বৈষম্য, এবং বিভাজনের মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে,
তখন বাংলাদেশে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো—একটা ভয়হীন সমাজ গড়া।
যেখানে মানুষ তার মত, বিশ্বাস, ভালোবাসা, এমনকি ভুল করার অধিকারটুকুও ধরে রাখতে পারে।
কারণ স্বাধীনতা মানে নিখুঁত হওয়া নয়—স্বাধীনতা মানে ভুল করার, আবার শেখার সুযোগ পাওয়া।
আমরা যদি সত্যিই উন্নত জাতি হতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হতে হবে ভয় থেকে মুক্ত হওয়া।
যে সমাজে মানুষ প্রশ্ন করতে পারে না, সেখানে কখনো অগ্রগতি হয় না।
যে রাষ্ট্র সমালোচনাকে অপরাধ মনে করে, সে রাষ্ট্র কখনো মানবিক হতে পারে না।
মানবাধিকারের ভিত্তি হলো—“মানুষের মর্যাদা।”
এই মর্যাদাকে আইনে নয়, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে।
মানবাধিকার তখনই বাস্তব হবে, যখন একজন মানুষ অন্যের কষ্টে কাঁদবে, অন্যের স্বাধীনতায় হিংসা নয়, গর্ব অনুভব করবে।
শেষ কথা:
বাংলাদেশের মানুষ অতীতে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে; এখন আমাদের লড়াই নিজের ভেতরের শৃঙ্খল ভাঙার।
ভয়ের সংস্কৃতি থেকে মুক্তি না পেলে, মানবাধিকার শুধু দিবস আর রিপোর্টের মধ্যে বন্দি থেকে যাবে।
আমাদের দরকার এমন এক সমাজ, যেখানে মানুষ নিঃশব্দে নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পারে—
“আমি মানুষ, তাই আমি স্বাধীন।”
লিখেছেন- Md Abdur Rahman
Writer, Blogger