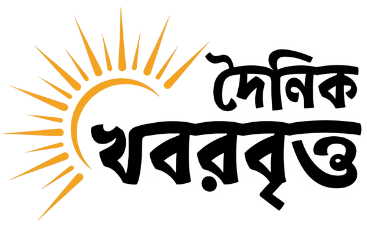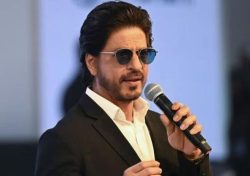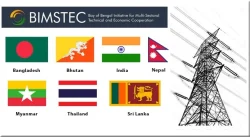মানুষের জন্মগত অধিকার নিয়ে কথা বলা এখন এক ধরনের সাহসিকতার নাম। রাষ্ট্র যখন তার নাগরিকের মুখের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করে, চিন্তাকে বেঁধে ফেলে আইনের বেড়িতে, তখন মানবাধিকার নিয়ে লেখা মানে কেবল তত্ত্ব নয়—একটি নৈতিক অবস্থান। বাংলাদেশে এখন মানবাধিকার নিয়ে কথা বললেই অনেকে চমকে ওঠে। কেউ ভাবে, এটা বিদেশি এজেন্ডা; কেউ ভাবে, এটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। অথচ বিষয়টা এতই সাধারণ যে, একজন শিশুর নিরাপদে বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার—সবই মানবাধিকারের আওতায় পড়ে।
কিন্তু আমাদের সমাজে এই ‘অধিকার’ শব্দটাই এখন আতঙ্কের কারণ।
মানবাধিকারকর্মী কিংবা লেখকরা এখন আর কেবল নীতি বা ন্যায়ের প্রশ্ন তুলছেন না—তারা বেঁচে থাকার অধিকারও হারাচ্ছেন। কারও কারও কণ্ঠ রুদ্ধ হয় আইন দিয়ে, কারও হয় গুম বা হুমকির মাধ্যমে। অথচ রাষ্ট্রের উচিত ছিল বিপরীত কাজটি করা—যাদের মতের সঙ্গে রাষ্ট্র একমত নয়, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
আমাদের রাষ্ট্র যেন ধীরে ধীরে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে মানবাধিকারের কথা বললেই সেটি রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে দেখা হয়।
ধর্মীয় স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা—এসব এখন তত্ত্বের চেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশে একটি চিন্তার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেটি কেবল একদল বা একধরনের মানুষের জন্য। তুমি যদি প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে ভাবো, ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রশ্ন করো, অথবা লিঙ্গ ও যৌনতা নিয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করো, তাহলে সমাজ তোমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, আর রাষ্ট্র তোমার পাশে নয়—প্রায়শই তোমার বিপরীতে দাঁড়াবে।
মানুষের সবচেয়ে বড় অধিকার হলো চিন্তা করার অধিকার। কিন্তু আজ এই অধিকারটাই সবচেয়ে সংকুচিত।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হেনস্তা, ধর্মীয় বিশ্বাসের নামে ছাত্রদের হয়রানি, কিংবা সামাজিক মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করে কারও কারও জীবনের নিরাপত্তা হারানো—এগুলো আলাদা ঘটনা নয়, বরং একটি সংস্কৃতির ফল। সেই সংস্কৃতি হলো ভয় ও নিষেধের সংস্কৃতি।
মানবাধিকার তখনই অর্থবহ হয়, যখন রাষ্ট্র তার সবচেয়ে দুর্বল নাগরিকের পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানে আমরা দেখি, রাষ্ট্র অনেক সময় শক্তিশালী গোষ্ঠীর ভয়েই নতি স্বীকার করে। ধর্মীয় চরমপন্থা ও সামাজিক আগ্রাসনকে রাষ্ট্রীয় নীরবতা আশ্রয় দিয়েছে।
বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু বাস্তবতার মাটিতে এগুলো কেবল লেখা শব্দ। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তখনই প্রকৃত হয়, যখন তুমি সরকারের বা সমাজের সমালোচনা করতে পারো, এবং তার পরও নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারো।
আজকাল অনেকেই বলে, “সবাইকে সম্মান করতে হবে”—এই কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকে ‘চুপ করে থাকো’। ধর্ম, যৌনতা, লিঙ্গ—এসব বিষয় নিয়ে কথা বলা মানেই এখন ঝুঁকি নেওয়া। অথচ সমাজ যতই ধর্মীয় বা নৈতিক হোক না কেন, মানুষ তার নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার রাখে।
একজন সমকামী মানুষ তার ভালোবাসা প্রকাশ করলে সেটা কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে—এই ধারণা নিজেই মানবাধিকারের পরিপন্থী। ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা করা, বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া নয়।
মানবাধিকারকে আমরা এখন দুই ভাগে ভাগ করেছি—‘আমাদের মতোদের’ ও ‘ওদের মতোদের’।
যে ব্যক্তি রাষ্ট্র বা ধর্মের প্রতিষ্ঠিত বয়ানকে প্রশ্ন করে, তার অধিকার যেন অর্ধেক হয়ে যায়। যেন তার নিরাপত্তা আর পুরো নাগরিকের মতো নয়।
আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে কেউ গালি দিলেই সেটা ‘ধর্মরক্ষার তাগিদ’, কিন্তু কেউ প্রশ্ন তুললেই সেটা ‘ধর্মঅবমাননা’। এভাবে ধীরে ধীরে আমরা এমন এক জগতে চলে যাচ্ছি যেখানে আইন ও ন্যায় নয়, ভয় ও ঘৃণা সিদ্ধান্ত নেয় কে মানুষ থাকবে আর কে নয়।
ধর্মীয় উগ্রতা কেবল মসজিদ বা মন্দিরের বিষয় নয়, এটি এখন প্রশাসনের চিন্তায় ঢুকে পড়েছে। পুলিশের বিবৃতি, প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, এমনকি আদালতের রায়েও দেখা যায় ধর্মীয় অনুভূতির চাপ। অথচ রাষ্ট্রের মূলনীতি হওয়া উচিত সবার প্রতি সমান আচরণ।
মানবাধিকার মানে কেবল রাজনৈতিক বন্দি মুক্ত করা নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনে মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। একজন নারী যখন কর্মক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হন, সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘন। একজন শ্রমিক যখন তার ন্যায্য মজুরি পান না, সেটাও মানবাধিকার লঙ্ঘন। কিন্তু এসব ঘটনা আমরা স্বাভাবিকভাবে নিতে শিখেছি। কারণ রাষ্ট্র কেবল তখনই সক্রিয় হয়, যখন আন্তর্জাতিক চাপ আসে।
তবে সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো—মানুষ এখন মানবাধিকার শব্দটাই ভয় পেতে শিখেছে।
যারা মানবাধিকারের কথা বলে, তাদের নামে মামলা হয়, নজরদারি হয়, অনেক সময় সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে নাগরিক সমাজে এখন একধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়েছে—‘যা ভাবো তা বলো না’।
এই ভয়ই সবচেয়ে বড় পরাজয়।
মানবাধিকার মানে কেবল অন্যের কথা বলার স্বাধীনতা নয়, বরং নিজের অস্বস্তিকর সত্য বলার অধিকারও। যে সমাজে ভিন্নমত সহ্য করা যায় না, সে সমাজের নৈতিক ভিত্তি ভেঙে যায়।
আজ যদি কেউ ধর্মীয় পাঠ্যবইয়ে প্রশ্ন তোলে কেন সেখানে নারীকে বারবার দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তাহলে তাকে বলা হয় নাস্তিক বা রাষ্ট্রবিরোধী। অথচ এই প্রশ্নই মানবাধিকারের মূল চেতনা—সবার সমান মর্যাদা।
যদি রাষ্ট্র সত্যিই ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত, তাহলে প্রতিটি নাগরিক তার বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও জীবনধারার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত। কিন্তু এখন ধর্মীয় অনুভূতির নামে রাষ্ট্রীয় দমননীতি চালু হয়েছে।
বাংলাদেশ মানবাধিকারের স্বাক্ষরকারী দেশ। আন্তর্জাতিক ঘোষণায় আমাদের নাম লেখা আছে, কিন্তু বাস্তবে আমরা এখনো ভয়, নিষেধ আর আত্মসমর্পণের দেশে।
মানুষকে শেখানো হচ্ছে—চুপ থাকাই নিরাপদ।
একজন সমকামী যদি প্রকাশ্যে ভালোবাসে, সে বিপদে পড়বে; একজন ব্লগার যদি ধর্মের সামাজিক ব্যবহার নিয়ে লেখে, সে গুম হবে; একজন নারী যদি নিজের শরীরের অধিকার দাবি করে, তাকে বলা হবে চরিত্রহীন।
মানবাধিকার এখানে কেবল শব্দ নয়, বরং একপ্রকার অভিযোগ—রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, আমাদের নিজের ভীরুতার বিরুদ্ধে।
আমাদের প্রয়োজন সাহসী রাষ্ট্র নয়, মানবিক রাষ্ট্র। এমন রাষ্ট্র, যা নাগরিককে শত্রু নয়, মানুষ হিসেবে দেখে। ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক মত, যৌনতা বা জীবনদর্শন—এসব কোনো কিছুই কারও মানবাধিকার কেড়ে নেওয়ার যুক্তি হতে পারে না।
মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো—তুমি তোমার মতো থাকবে, আমি আমার মতো, এবং আমরা দুজনই নিরাপদ থাকব।
কিন্তু আমরা আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে এই সহজ বাক্যটাই বিলাসিতা মনে হয়।
রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকের কণ্ঠ শুনতে ভয় পায়, তাহলে সেই রাষ্ট্র শক্তিশালী নয়, দুর্বল।
মানুষ যদি নিজের অধিকারের কথা বলতে ভয় পায়, তাহলে সেই সমাজ সভ্য নয়, কেবল ভীরু।
শেষ কথা:
মানবাধিকার কোনো বিদেশি চিন্তা নয়। এটি মানুষের জন্মগত মর্যাদা রক্ষার মৌলিক শর্ত। রাষ্ট্র যদি সত্যিই টিকে থাকতে চায়, তাহলে তাকে তার নাগরিকের ভয় দূর করতে হবে, তার কণ্ঠ ফিরিয়ে দিতে হবে।
কারণ ইতিহাস বলে—যে রাষ্ট্র মানুষকে নীরব করে রাখে, শেষ পর্যন্ত সেই রাষ্ট্রই নিজের নীরবতায় ডুবে যায়।