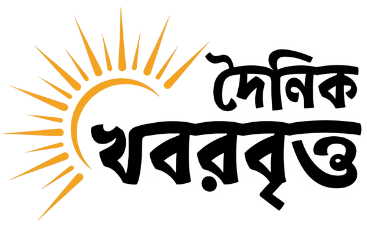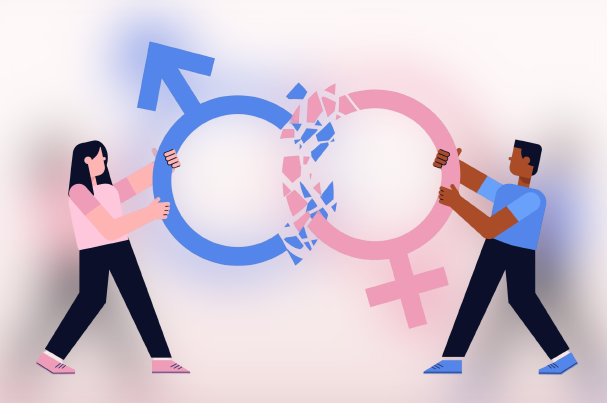স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ নারীর অধিকার ও শিশুদের সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বেড়েছে, নানা নীতি ও আইন প্রণীত হয়েছে তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে। তবুও একটি মৌলিক সমস্যা এখনও বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোতে দৃশ্যমান—পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ। এর কারণে লিঙ্গ-ন্যায়বিচার বা gender justice অর্জনের পথে এখনও বড় বাধা রয়ে গেছে।
পিতৃতন্ত্র বনাম লিঙ্গ-ন্যায়বিচার
লিঙ্গ-ন্যায়বিচার বলতে বোঝায়, কারও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান অধিকার, সুযোগ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অন্যদিকে, পিতৃতন্ত্র হলো এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব মূলত পুরুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে—হোক তা নৈতিক নেতৃত্ব, সম্পদের মালিকানা বা সামাজিক সুবিধা। ইতিহাস, সংস্কৃতি, শ্রেণি ও বর্ণভিত্তিক বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার মূল ভিত্তি হিসেবেও পিতৃতন্ত্র কাজ করে।
বাংলাদেশে বাস্তব চিত্র
নারীরা এখনও জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন—পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা জনপরিসরে।
- পারিবারিক সহিংসতা ও যৌতুকজনিত নির্যাতন: প্রায়ই ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা পরিবারের সদস্যের হাতেই নারীরা শারীরিক, মানসিক বা মৌখিক নির্যাতনের শিকার হন। যৌতুক না দেওয়ার ঘটনা এখনও অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা কিংবা আত্মহত্যার কারণ হয়।
- যৌন সহিংসতা ও পাচার: হেফাজতে ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধ বেড়েছে। একইসঙ্গে নারী পাচার এখনও একটি গুরুতর সমস্যা।
- আত্মহত্যা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্যানুযায়ী, আত্মহত্যা বিশ্বব্যাপী লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার একটি অবহেলিত রূপ। বাংলাদেশে যৌতুক-নির্যাতনের শিকার নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনকভাবে বেশি।
- শিশুশ্রম ও বঞ্চনা: গৃহকর্মী বা কারখানায় মেয়েশিশুরা শারীরিক ও মানসিক চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়ে।
- পথশিশুর ঝুঁকি: ইউনিসেফের ২০২৪ সালের গবেষণা অনুযায়ী, ঢাকাসহ সারা দেশে প্রায় ৩৪ লাখ শিশু রাস্তার পাশে বসবাস করছে। তারা নানা ধরনের শোষণ, যৌন সহিংসতা, পাচার ও বিপজ্জনক শ্রমে নিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য
অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক মেয়ে শিশু এখনও তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে না। এর ফলে নারীদের সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে আছে। কর্মক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্য, কম মজুরি এবং নেতৃত্বে সীমিত প্রতিনিধিত্বের শিকার হচ্ছেন।
সমাধানের দিক নির্দেশনা
- বাধাগ্রস্ত মানসিকতা ভাঙা: লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বন্ধে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করাই মূল কাজ।
- নীতিগত উদ্যোগ: অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন এবং এগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন জরুরি।
- শিক্ষা ও সচেতনতা: শিক্ষিত নারী সমাজকে চ্যালেঞ্জ করার, নিজের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার পথ তৈরি করে।
- কর্মক্ষেত্রে সমতা: সংগঠনগুলোতে নারীদের অভিজ্ঞতা শুনতে হবে এবং তাদের নেতৃত্বে জায়গা করে দিতে হবে।
- আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ-ন্যায়বিচার আন্দোলন প্রমাণ করছে, সংলাপ, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ এই পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি।
উপসংহার
বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই নারী ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার পথে একধাপ এগিয়েছে। তবে বাস্তব পরিবর্তন আনতে হলে সমাজে দীর্ঘদিনের প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙতে হবে। পরিবার থেকে রাষ্ট্রের নীতি পর্যন্ত—প্রতিটি স্তরে নারীর কণ্ঠকে স্বীকৃতি দেওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানও নিতে হবে।
লিঙ্গ-ন্যায়বিচার কেবল নারীর জন্য নয়—পুরো সমাজের জন্য সমতার ভিত্তি। আর এই যাত্রায় সহযোগিতা, সংহতি ও সচেতন অংশগ্রহণই পারে একটি ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।