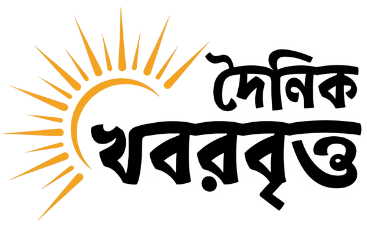২০২৫ সালের ২২ আগস্ট বাংলাদেশের বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকা—যার মধ্যে দ্য ডেইলি স্টারও রয়েছে—খবর প্রকাশ করে যে ২৭ বছর বয়সী দুর্জয় চৌধুরী পুলিশের হেফাজতে মারা গেছেন। মাত্র একদিন আগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশের দাবি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়: যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের হেফাজতে জীবিত অবস্থায় প্রবেশ করেন, তবে তার মৃত্যু—even আত্মহত্যা—কীভাবে কেবল ব্যক্তিগত দায় হয়ে যায়? রাষ্ট্র কি তবে দায়মুক্ত হয়?
২০১৩ সালের আইন ও এর সীমাবদ্ধতা
জাতিসংঘের কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার (CAT) কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে ২০১৩ সালে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিরোধ) আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন প্রণীত হওয়ার সময় এটিকে নাগরিক সমাজ একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে স্বাগত জানায়। কারণ, আইনের শিরোনাম ও প্রস্তাবনায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্যাতন এবং অবহেলা—উভয় কারণেই হেফাজতে মৃত্যু প্রতিরোধের ব্যাপারে।
কিন্তু বাস্তবে আইনের অপরাধসংক্রান্ত ধারা সীমিত। আইনটির ১৩ ও ১৫ ধারা কেবল নির্যাতন বা নির্যাতনজনিত মৃত্যুকেই অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ—
- হেফাজতে আত্মহত্যা,
- চিকিৎসার অভাব,
- বা কারাগারের অবহেলাজনিত মৃত্যু—
এসব ক্ষেত্রে কোনো ফৌজদারি দায় এ আইনে নির্ধারিত নয়। ফলে মৃত্যুর সংজ্ঞা ও দায়ের প্রশ্নে আইনের সুরক্ষা থেমে যায় ঠিক সেখানেই, যেখানে সবচেয়ে জরুরি।
আন্তর্জাতিক ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা
আন্তর্জাতিক আইনে বিষয়টি স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের (ICCPR) ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ জীবনরক্ষার অধিকারকে অব্যাহতি অযোগ্য (non-derogable) অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি বহুবার উল্লেখ করেছে, হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে এবং দেখাতে হবে যে তারা মৃত্যু প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছিল।
বাংলাদেশের সংবিধানও একইভাবে জীবনের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে। BLAST বনাম বাংলাদেশ (২০০৩) মামলায় হাইকোর্ট রায়ে বলেছিল, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু সংবিধানের ৩১ এবং ৩২ অনুচ্ছেদে জীবনরক্ষার অধিকারের পরিপন্থী। অর্থাৎ, কেউ একবার রাষ্ট্রীয় হেফাজতে গেলে তার জীবনরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে।
কমন ল’ এবং তুলনামূলক রায়
ব্রিটিশ আইনও, যা এখনও বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় প্রভাব রাখে, একই নীতি প্রতিপন্ন করে। ২০০০ সালের Reeves বনাম Commissioner of Police মামলায় এক বন্দি আত্মহত্যা করলে পুলিশকে দায়ী করা হয়। অনুরূপভাবে, Kirkham বনাম Chief Constable (1990) মামলায় আত্মহত্যাপ্রবণ বন্দির নিরাপত্তা না দেওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ দায়ী হন। এসব মামলায় বলা হয়, কারও হেফাজত মানেই তার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, আর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আসে দায়বদ্ধতা—শুধু নির্যাতন নয়, সম্ভাব্য আত্মক্ষতিসহ যেকোনও ক্ষতির জন্যও।
বিকল্প প্রতিকার ও সীমাবদ্ধতা
যেহেতু ২০১৩ সালের আইন অবহেলাজনিত মৃত্যু অন্তর্ভুক্ত করেনি, তাই ভুক্তভোগীর পরিবারকে অনেক ক্ষেত্রে সংবিধানগত প্রতিকার বা টর্ট আইনের ওপর নির্ভর করতে হয়।
- CCB ফাউন্ডেশন বনাম বাংলাদেশ (২০১৬) মামলায় হাইকোর্ট জননিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের অবহেলায় জীবনের অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বলে রায় দিয়ে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।
- বানো বনাম বাংলাদেশ (২০২০) মামলাতেও বেআইনি আটকাদেশের কারণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।
কিন্তু বাংলাদেশের টর্ট আইন এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক, জটিল, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘসূত্রতায় ভুগছে। ফলে অনেক পরিবার ন্যায়বিচারের বাস্তব সুযোগ পান না।
প্রয়োজনীয় সংস্কার
আইনকে কার্যকর করতে হলে অবহেলাজনিত বা আত্মহত্যাজনিত—সব ধরণের হেফাজতে মৃত্যুকেই স্পষ্টভাবে আলাদা অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রমাণের দায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর স্থানান্তর করতে হবে, যাতে তারা দেখাতে বাধ্য হয় যে মৃত্যুরোধে যৌক্তিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তদন্ত অবশ্যই স্বাধীন সংস্থা দ্বারা সম্পন্ন হতে হবে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ দ্বারা নয়। পাশাপাশি, টর্ট জুরিসপ্রুডেন্সকে বিকশিত করে ক্ষতিপূরণপ্রক্রিয়াকে সহজলভ্য করতে হবে।
উপসংহার
দুর্জয় চৌধুরীর মৃত্যু কেবল একটি তরুণ জীবনের অপচয় নয়—এটি ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের জন্য এক প্রমাণ পরীক্ষা। রাষ্ট্র যেদিন কাউকে হেফাজতে নেয়, সেদিন থেকেই তার জীবন ও নিরাপত্তার পূর্ণ দায়ভার রাষ্ট্রের কাঁধে পড়ে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিচারব্যবস্থা স্পষ্ট করেছে যে অবহেলা দায় এড়ানোর অজুহাত হতে পারে না। এখন সময় এসেছে সংসদের আইন সংস্কার এবং আদালতের প্রতিকার আরও প্রসারিত করার।