‘’পাহাড়ে যৌন সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার অনুপস্থিত, আর রাষ্ট্রীয় নিষ্ক্রিয়তা সেই অপরাধকেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।‘’
পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক ধর্ষণ, সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় যে ভয়ংকর বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে, তা এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—এটি রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার এক দীর্ঘস্থায়ী কাঠামো। খাগড়াছড়ির গুইমারায় এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পর স্থানীয়দের প্রতিবাদে গুলিবর্ষণ এবং তিনজনের মৃত্যু সেই কাঠামোর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। এই মৃত্যু আকস্মিক নয়; এটি বহু বছরের অবহেলা, দায়হীনতা ও নিরাপত্তাহীনতার ফল।
রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল ভুক্তভোগীকে সুরক্ষা দেওয়া এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা। কিন্তু বাস্তবতা হলো—ধর্ষকরা রয়ে গেছে অদৃশ্য সুরক্ষার ছত্রছায়ায়, আর যে জনগোষ্ঠী ন্যায়বিচার দাবি করেছে তারা পরিণত হয়েছে লক্ষ্যবস্তুতে। পাহাড়ে বিচার না পাওয়া এখন কেবল একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, এটি এক প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতা যা অপরাধীদের পক্ষেই কাজ করে।
পাহাড়ে ধর্ষণ এখন ভয়ের নয়, নিয়মিত বাস্তবতা
পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য বলছে, গত এক দশকে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শতাধিক ঘটনা ঘটেছে—এবং এর বেশির ভাগ মামলাই নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় ঝুলে আছে। ডিএনএ না মেলা, ডাক্তারি রিপোর্টে ‘প্রমাণ নেই’ বলা, বা প্রভাবশালী আসামিদের চাপের মুখে মামলা দুর্বল করে দেওয়া—এসব এখন এক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।
একজন প্রতিবন্ধী আদিবাসী নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ১২ জন আসামি গ্রেপ্তার হলেও ডিএনএ পরীক্ষার অজুহাতে তারা সবাই জামিনে ছাড়া পায়। খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে একাধিক মারমা কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা গেছে—অভিযোগ ওঠার পর তদন্ত শুরু হলেও দ্রুত তা থমকে গেছে। প্রশাসনিক তৎপরতা সেখানে কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থেকেছে।
এই প্রক্রিয়া কেবল বিচারকে অকার্যকর করে না; বরং অপরাধীদের জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়—“পাহাড়ে ধর্ষণ করলেও শাস্তি নেই।”
প্রশাসন ও নিরাপত্তা কাঠামোর উদাসীনতা
যেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল বিচার নিশ্চিত করা, সেখানে দেখা যাচ্ছে উল্টো প্রবণতা। পাহাড়ে ধর্ষণের ঘটনায় মামলা করতে গেলে পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে ‘সমঝোতা’র পরামর্শ দেয়। মামলার কাগজপত্র দুর্বল করে ফেলা, ভুক্তভোগী পরিবারকে ভয় দেখানো, অথবা সমাজপতিদের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা—এসব সাধারণ চর্চায় পরিণত হয়েছে। প্রশাসন কার্যত দায় এড়িয়ে যাচ্ছে, যেন এই অপরাধগুলো রাষ্ট্রের আওতার বাইরে পড়ে।
গুইমারার ঘটনায় ধর্ষণের বিচারের দাবিতে যারা রাস্তায় নেমেছিল, তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। নিহতদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল না, কিন্তু বিচার চাইতে গিয়েই তারা প্রাণ হারাল। নিহতদের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়নি, কিন্তু প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে এক হাজারের বেশি মামলা হয়েছে। এই পরিস্থিতি কি রাষ্ট্র পরিচালনার পরিচায়ক, নাকি প্রতিশোধমূলক শক্তি প্রয়োগের উদাহরণ?
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর দায়িত্ব নাগরিকের সুরক্ষা, কিন্তু পাহাড়ে সেই বাহিনী ভুক্তভোগীদের বদলে অভিযুক্তদের রক্ষা করছে—এমন অভিযোগ স্থানীয় ও জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবেদনে প্রতিনিয়ত উঠে আসছে।
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যানই রাষ্ট্রের দায়ের প্রমাণ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) হিসাব অনুযায়ী, শুধু ২০২৪ সালেই ২০০টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এতে ২১ জন নিহত, অসংখ্য ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে। দুই হাজার একরের বেশি ভূমি দখল হয়েছে বিভিন্নভাবে। এই ঘটনার একটিরও সুষ্ঠু তদন্ত বা বিচার হয়নি। প্রশাসন বা সরকারিভাবে এসব অপরাধের দায় স্বীকার তো দূরের কথা, বরং বিষয়গুলোকে ‘স্থানীয় উত্তেজনা’ বা ‘সাময়িক সংঘাত’ হিসেবে আড়াল করা হয়েছে।
এই ব্যর্থতা কেবল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সংকট নয়, এটি সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা ও অধিকারের প্রতি রাষ্ট্রের দায়হীনতার বহিঃপ্রকাশ। আদালত, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনিক কাঠামো যদি মিলিতভাবে ন্যায়বিচার ঠেকায়, তাহলে সেটি দুর্ঘটনা নয়—ইচ্ছাকৃত শাসনপদ্ধতির ইঙ্গিত।
দায় এড়ানোর সময় শেষ
পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনায় রাষ্ট্রীয় নিষ্ক্রিয়তা কেবল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকেই বিপন্ন করেনি; বরং বিচারপ্রার্থীদের রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই বিচ্ছিন্নতাই সবচেয়ে বড় হুমকি।
সংবিধান রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে প্রতিটি নাগরিকের জীবন, মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিতে। অথচ পাহাড়ে এই দায়িত্ব পালন তো দূরের কথা, এখানে রাষ্ট্রের উপস্থিতি অনেক সময় ভয়, গুলিবর্ষণ বা মামলা দায়েরের মাধ্যমে অনুভূত হয়। সংখ্যালঘুর প্রতি দায়িত্ব পালন না করলে রাষ্ট্রের নৈতিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়—এই সত্য এড়ানো সম্ভব নয়।
জরুরি রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ এখনই প্রয়োজন
১. ধর্ষণ মামলার তদন্ত ও বিচারের জন্য বিশেষায়িত ইউনিট গঠন
২. পুলিশ ও প্রশাসনকে জবাবদিহির আওতায় আনা
৩. ডিএনএ ও ফরেনসিক তদন্তে বিলম্ব ও কারচুপি বন্ধ
৪. পার্বত্য নারীদের নিরাপত্তায় দ্রুত নীতিগত হস্তক্ষেপ
৫. মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত
ন্যায়বিচার শুধু আদালতে বসে নয়—রাষ্ট্রকে ইচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়। পাহাড়ে ধর্ষণ ও দমননীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যদি নীরব থাকে, তবে সেই নীরবতা আর নিরপেক্ষতা নয়; তা হবে অপরাধের সহায়তা।
উপসংহার
পাহাড়ের মানুষের জীবন এখন আইনের সুরক্ষায় নয়, বরং ভয় ও অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। যারা বিচার চায় তারা মামলার আসামি হয়, আর যারা অপরাধ করে তারা আইনের ছায়ায় নিরাপদ থাকে। এই কাঠামো ভাঙা না গেলে পাহাড়ে নাগরিকত্ব আর রাষ্ট্রীয় আস্থা—দুটোই ধ্বংস হবে।
লিখেছেনঃ Md. Emdadul Hoque Chowdhury
মানবাধিকার কর্মী ও লেখক
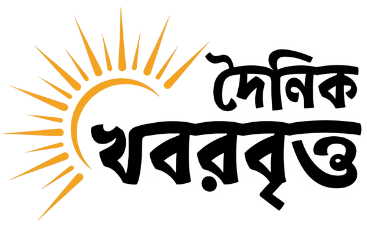


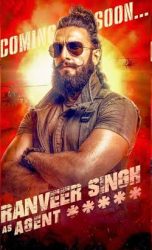











One Response
এই বক্তব্যটি আবেগনির্ভর এবং একধরনের সাধারণীকরণ করেছে। এখানে পাহাড়ের জটিল সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত বাস্তবতাকে একপাক্ষিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। “আইন নেই, সবাই ভয় ও অভিজ্ঞতার উপর বাঁচে” — এই ধরনের সার্বিক মন্তব্য বাস্তব পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিত করে। সমালোচনায় সমস্যার বিশ্লেষণ থাকলেও কোনো গঠনমূলক সমাধান বা বাস্তবভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে এটি সচেতন আলোচনার পরিবর্তে হতাশা সৃষ্টির মতো মনে হয়।