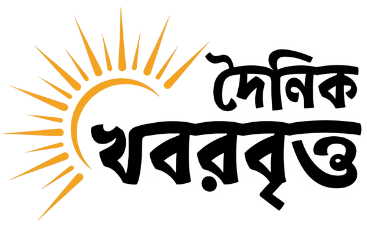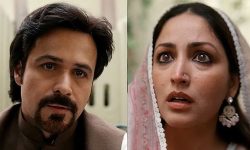ঢাকার রাস্তায় হেঁটে গেলে মানুষ প্রায়ই বলে, “এই সমাজ আর আগের মতো নেই।” কেউ মনে করেন মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার কেউ মনে করেন মানুষ ধর্মের নামে একে অপরের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। দু’টির মাঝখানে যে বাস্তবতা দাঁড়িয়ে আছে, তা হলো—বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সমাজগুলো ক্রমশ একটি নীরব, কিন্তু তীব্র ধর্মীয় উগ্রবাদের আগুনে পুড়ছে। এই আগুন শুধু রাজনৈতিক নয়, এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পারিবারিক পরিসরেও ছড়িয়ে পড়ছে।
ধর্মীয় উগ্রবাদ শব্দটি শুনলেই অনেকে মনে করেন, ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত। ধর্ম নিজে কখনোই উগ্র নয়; উগ্র হয় মানুষ, যারা ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতা, প্রভাব বা প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে। ঢাকার একটি কলেজে কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা মনে আছে—একজন শিক্ষককে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ছাত্রদের একাংশ ক্লাস থেকে টেনে বের করেছিল। পরে দেখা গেল, তিনি শুধু সাহিত্য পাঠের সময় একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যা কিছু গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে মেলেনি। এটাই হলো আজকের বাস্তবতা: ধর্মের ভাষায় রাজনীতি, রাজনীতির ভাষায় ধর্ম।
পরিবার থেকে মসজিদ পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি জায়গা যখন ভিন্নমতের প্রতি সহনশীল নয়, তখন একটি প্রজন্ম আসে যাদের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি জন্মায়। আমি একবার এক ষোলো বছর বয়সী মাদরাসা ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে বলল, “আমার শিক্ষক বলেছেন, যারা ভিন্নমত পোষণ করে, তারা শত্রু।” আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি কি কখনও ভিন্নমত শুনেছো?” সে চুপ করে বলল, “না, শুনলে হয়তো আমার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।” এই উত্তর শুনে আমি ভয় পাই। কারণ এটি কেবল ওই ছেলের নয়, এটি এক প্রজন্মের ভয়—যেখানে ভিন্ন মত শোনা মানেই বিশ্বাস নষ্ট হওয়া।
ইন্টারনেটের যুগে উগ্রবাদ আরও ভয়ানক রূপ নিয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো—যেমন YouTube, Facebook, Telegram—এতে উগ্রবাদী বক্তাদের কনটেন্টের হাউজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা বলছে, “এই পৃথিবী আমাদের বিরুদ্ধে,” “আমরা আক্রান্ত,” “ধর্ম রক্ষা করতে যুদ্ধ করতে হবে।” এই কথাগুলো এক কিশোরের মনে ‘মিশন ভাবনা’ তৈরি করে, যেখানে সে নিজেকে একজন ‘সৈনিক’ হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, নাম-পরিচয়হীন কনটেন্ট এবং ছাপিয়ে যাওয়া উগ্রতার কারণে সে অনুপ্রাণিত হয়। ২০২৩ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার ১৮–২৫ বছর বয়সী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ২২ শতাংশ অন্তত একবার ‘ধর্মীয় যুদ্ধ’ বা ‘খিলাফতের আদর্শ’ সম্পর্কিত কনটেন্ট দেখেছে। এর মধ্যে প্রায় ৯ শতাংশ বলেছে, তারা সেই ভিডিও দেখে “অনুপ্রাণিত” হয়েছে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতেও ধর্মীয় উগ্রতার ব্যবহার বেড়েছে। ধর্মীয় সংগঠনগুলো এখন শুধু মসজিদের ভিতর নয়, রাজনৈতিক অঙ্গনেও সক্রিয়। তারা নির্বাচন, আন্দোলন, এবং সামাজিক বয়ানগুলোতে ধর্মের আবেগকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় দেখা গেছে—একটি মসজিদের ইমাম নির্বাচনের বিরোধে সংঘর্ষে জড়িত হয়। কিন্তু বিষয়টি শুধুই ধর্মীয় ছিল না; পেছনে ছিল রাজনৈতিক দখল, তহবিল এবং ভোটের হিসাব। ধর্ম সেখানে কেবল মুখোশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
উগ্রবাদ এবং ধর্মান্ধতার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় মধ্যপন্থী মুসলমানদের। যারা বিশ্বাস করে ধর্ম মানে শান্তি, সহাবস্থান এবং মানবিকতা—তাদের কণ্ঠ চাপা পড়ে। ফলে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়, সংলাপের জায়গা সংকুচিত হয়। বিশেষত নারীদের ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে প্রকট। উগ্রবাদ নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে আঘাত করে। মেসেজগুলো যেমন—“মেয়েরা ঘরে থাকো,” “নারী নেতৃত্ব হারাম”—এগুলো প্রচার করা হয় ধর্মের ব্যাখ্যার নামে, অথচ ধর্মের মৌলিক শিক্ষা থেকে এর সামান্য সম্পর্কও নেই।
আমরা দেখি, একজন নারী সাংবাদিক বা কর্মী শুধু ধর্ম নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই তাকে ‘অবিশ্বাসী’ বা ‘বিপথগামী’ বলা হয়। এটি প্রমাণ করে যে উগ্রবাদ কেবল মসজিদে নয়, আমাদের ভাষা ও চিন্তার ভেতরও ঢুকে গেছে।
ধর্মীয় উগ্রবাদ মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় ভুল হলো প্রতিতর্কের মাধ্যমে যুদ্ধ করা। উগ্রবাদ যুক্তি দিয়ে পরাজিত হয় না; এটি পরাজিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। একজন কিশোর যখন ইসলামী ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞানের প্রকৃত সম্পর্ক বুঝতে শেখে, তখন সে বুঝতে পারে—ধর্ম কখনো ঘৃণা শেখায় না। সেই শিক্ষা আসতে পারে পাঠ্যক্রমে সংস্কার, ইতিহাসে মুক্ত আলোচনা এবং ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্বশীল ব্যাখ্যা থেকে। আমরা প্রায়ই ভুল করি, ধর্ম মানে শুধুই আনুগত্য; কিন্তু ধর্ম মানে প্রশ্ন করার অধিকারও রয়েছে।
রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। উগ্রবাদ দমন শুধু পুলিশের কাজ নয়; এটি নীতিগত অবস্থানও দাবি করে। যখন সরকার ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে ভোটের রাজনীতিতে ব্যবহার করে, বার্তা যায়—উগ্রতা কৌশল। এই কৌশল স্বাভাবিক হয়ে গেলে মানুষ মনে করে, “সবাই তো ধর্মের নামে রাজনীতি করছে, আমি কেন না করব?” রাষ্ট্রকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে—ধর্ম ব্যক্তিগত, উগ্রবাদ অপরাধ।
আজ আমরা “ধর্মীয় মানুষ” আর “ধর্মান্ধ” এই দুইয়ের পার্থক্য ভুলে যাচ্ছি। যিনি অন্যের প্রতি সহনশীল, ন্যায্য, সহমর্মী—তিনি ধর্মীয়। যিনি নিজের বিশ্বাস চাপিয়ে দেন, অন্যকে ঘৃণা করেন—তিনি ধর্মান্ধ। এই পার্থক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এখন জরুরি। সমাজ তখনই টিকে, যখন মানুষ একে অপরকে ‘মানুষ’ হিসেবে দেখে, ‘বিশ্বাস’ হিসেবে নয়।
ধর্মীয় উগ্রবাদ কখনো হঠাৎ আসে না; এটি আসে অসহিষ্ণু সমাজ, দুর্বল শিক্ষা, ভয়ের রাজনীতি এবং অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে। আজ যদি আমরা ভয়ের সংস্কৃতি স্থাপন করি, আগামী প্রজন্ম কেবল অন্ধকার উত্তরাধিকার পাবে। সময় এসেছে ধর্মকে নয়, তার মানবিক অর্থকে ফিরিয়ে আনার। ধর্ম মানুষকে বিভাজন করে না; মানুষই ধর্মকে বিভাজনের অস্ত্র বানায়। সিদ্ধান্ত আমাদের—সহাবস্থানের সমাজ চাই, নাকি বিভাজনের রাজনীতি?
লিখেছেন- Md Abdur Rahman
Writer, Blogger